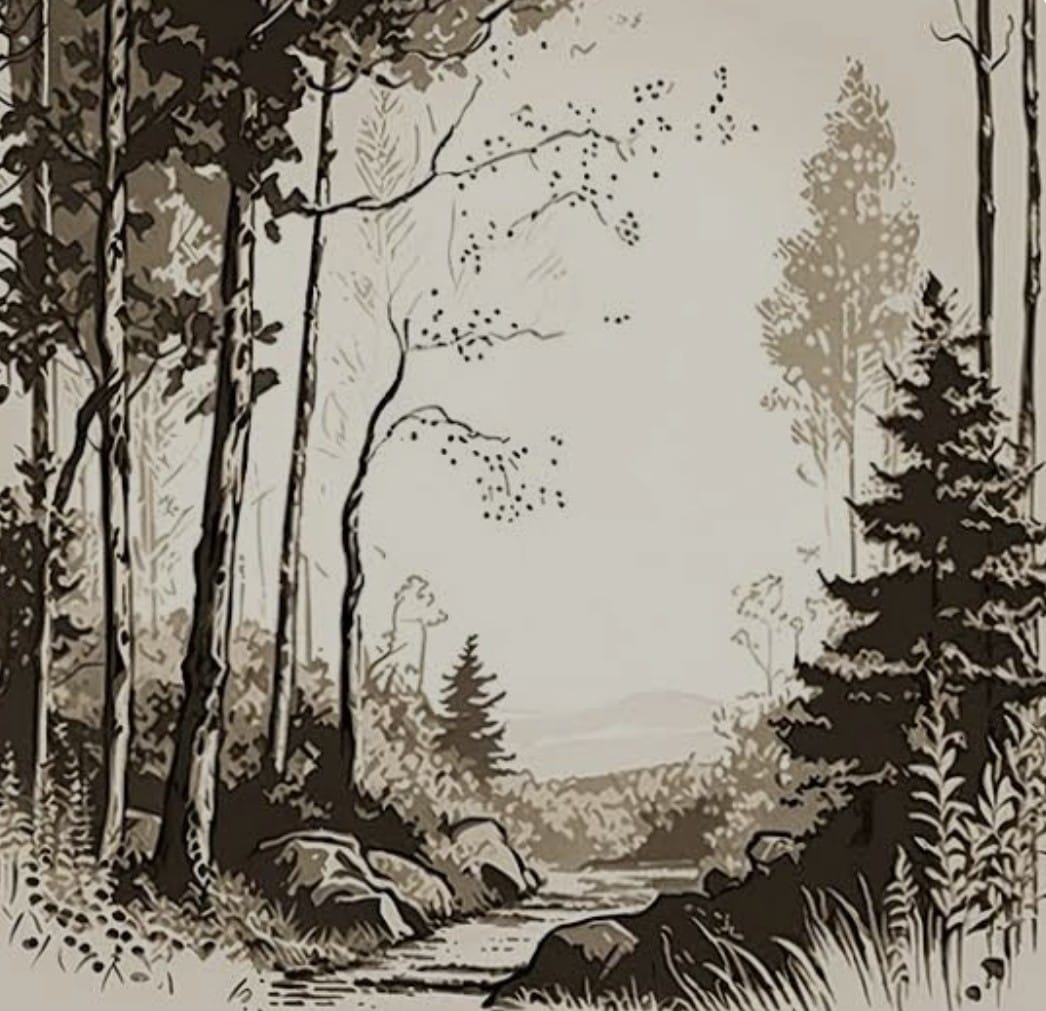পঞ্চবাহু
কোনো এক কালে, তৎকালীন সভ্যতার মানুষজন, হারিনী এবং ইয়াঝিনী নাম্নী দুই নদীর সঙ্গমস্থলের নাম রেখেছিল গুপ্তগামিনী। সে সভ্যতা অন্তর্হিত হয়ে অরণ্যের গর্ভে চলে গেলেও, সেই নাম থেকে গেছে সঙ্গমস্থলের স্মারকমৃত্তিকাতটে। গ্রীষ্মে দু-পাশেই তিরতির করে ক্ষীণ ধারা বয়ে চলে। আর আষাঢ়ে ফিরে পায় যৌবন। প্লব যে কী বিচিত্র প্রপঞ্চ, ঋতু পরিবর্তন বুঝিয়ে দিয়ে যায়।
তাদের অতিক্রম করে কিছুটা এগোলে বিস্তীর্ণ এবং গহন অরণ্যভূমি, অরণ্য গিয়ে মেশে গিরিশৃংখলে… সেই নীলচে মেঘের মতো পাহাড়ের কোলে এক উপত্যকায় গিরিরাজ্য নরসিংহপুর।
সহস্রাব্দ পূর্বে, গিরি অঞ্চলের প্রতিপালক দ্রাবিড়ীয় নৃপতি নিজের রাজ্য পঞ্চভূত উৎসর্গ করেছিলেন শ্রী নরসিংহদেবকে। সেই থেকে এই নাম।
নরসিংহপুরের প্রান্তে, নগরীর শেষ জনপদের কুটির-রেখা অতিক্রম করে গিরিপথ বাঁক নিয়ে নামতে শুরু করে অন্য এক বিচ্ছিন্ন পল্লী অঞ্চলে। দ্রাবীড়িও ভূমিপুত্রদের অঞ্চল, নগরীর কাছে অন্ত্যজ।
কস্মিনকালে কেউ সেই পাহাড়ী গ্রামগুলির দিকে এগোলে অনুভব করে– প্রকৃতি কীভাবে হঠাৎই রূপ পরিবর্তন করতে পারে। কাছাকাছি থেকেও পাহাড়ের এক পিঠের থেকে অন্য পিঠের সভ্যতা কতটা পৃথক হয়ে আছে। চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য, কখনো উজ্জ্বল… কখনো কুয়াশাচ্ছন্ন। ধূমরাশি গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায় উতরাই বেয়ে, উপত্যকা ছুঁয়ে… এক ধাপ নীচে ছোটো ছোটো পর্ণকুটিরের দিকে। ভিজে কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে যায় একা অথবা শ্রেণীবদ্ধ নারী। বৃদ্ধেরা অপেক্ষা করে দ্বিপ্রহরের… হয় সূর্যের তেজ বাড়বে, নাহলে কাঠের আর্দ্রতা কমে অগ্নি সংযোগের উপযোগী হবে। নগরী থেকে যদিও বা কেউ আসে… অশ্বে অথবা গর্ধব-পৃষ্ঠে, অন্ত্যজদের সেথায় প্রবেশের অনুমতি নেই। দুধ, মধু, অথবা জঙ্গলের কাঠও তারা নিয়ে যেতে পারে না। রাজ্য থেকে কেউ এসে নিয়ে যায়, নাম মাত্র দ্রব্যমূল্য অথবা পারিশ্রমিক। না দিলে, এমনিই লুঠে নিয়ে যেতে পারে রাজকর্মচারী। অস্পৃশ্যদের থেকে কিছু নিতে গেলেও কিছু নিয়ম মানতে হয়। কিছু নির্দিষ্ট বর্ণের ব্যক্তিই আসে রাজ্য থেকে। এবং উভয়পক্ষে কর্তব্য সমাপন করে ফিরে যায়, সে ফেরারও আচরণ বিধি আছে। তবে, এসব নিয়ম মানুষের। শুদ্ধিকরণ হলে, সামগ্রীর দোষ থাকে না। একবার শ্রী নরসিংহদেবকে উৎসর্গ করলে– সবই মহাপ্রসাদ।
এই ক্ষুদ্র দ্রাবিড়ীয় পল্লী এবং গিরি-শৃংখল জুড়ে এমন অনেক ছোটো ছোটো গ্রামের থেকে পাওয়া রসদেই উষ্ণ হয় নরসিংহপুর, উষ্ণ হয় রাজ অন্তঃপুর, উষ্ণ হয় আরাধ্য নরসিংহদেবের মন্দির।
নরসিংহপুরের অনতিদূরে এই অখ্যাত দ্রাবিড়ীয় পল্লীতেই এক পঞ্চবাহু সরোবর– পাহাড়ের শরীরে তার পাঁচটি বাহু পাঁচদিকে চলে গেছে… এক অদ্ভুত জলজপ্রাণীর মতো, পাহাড়ের শরীরে এক জাদুসম্ভব নক্ষত্রের রেখে যাওয়া জন্মদাগের মতো। তার পাশ দিয়ে ধীর গতিতে চলে যায় প্রার্থনারত শ্রমণদের সারিবদ্ধ দল। তার পাশ দিয়ে ধীর গতিতে চলে যায় বিশাল-বপু গৌর। তার ওপরে ঝুঁকে পড়ে জল খেয়ে যায় পাহাড়ী চিতা, মহাশৃংগ শম্বর। জ্যোৎস্নায় রূপোর মতো, দ্বিপ্রহরের সোনার মতো… চকচক করে সেই সরোবরের জল। অথচ তার স্বচ্ছতা কম, পান্নাসবুজ জলে সবসময়ে হালকা ঢেউ তিরতির করে ওঠে পাহাড়ী বাতাসের স্পর্শে।
তার এক বাহুর কাছে ভূমিপুত্রদের আরাধ্যা বনদেবীর থান। দেবীর নাকে বড়ো পেতলের নথ, শরীর রক্তবর্ণ। মোহিনী ভাস্কর্য নয়… দীঘল নেত্রা, পৃথুলকায়া অরণ্যের মহামায়া।
তার আর এক বাহুর কাছে নিষাদদের কুটির। সেখানে প্রতিদিনই কেউ না কেউ অস্ত্রে শান দেয়, অথবা কোনো শিকার করে আনা প্রাণীর চর্ম শুকোতে দেয় আগুনের তাপে।
আর তার গহন অরণ্যের কাছে চলে যাওয়া বাহুটির কাছে সৎকারভূমি। সেখানে বংশ পরম্পরায় সৎকারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এক পরিবার। এই পল্লীতে সমাধী হয় না, দাহ হয় অধিবাসীদের দেহ। অস্থি নিরঞ্জন হয় সরোবরের তৃতীয় বাহুতে। সেখানে এখন অবশিষ্ট একজন প্রৌঢ়, এবং তার একমাত্র কন্যা আধিরা।
তার চতুর্থ বাহুও এক নির্জন অঞ্চল, কয়েকজন শ্রমণ মিলে কুটিরনির্মাণ করে বসবাস করেন। মাঝেমাঝে মাধুকরী উপলক্ষে পল্লী অঞ্চলে এলেই তাঁদের দেখা যায়। কথা হয় না। মাথা নত করে চলে যান পাশ দিয়ে এক এক করে।
চার বাহুর পাশ থেকেই ধোঁয়া উঠতে থাকে আকাশের দিকে। কোথাও ক্ষীণ… কোথাও প্রবল। চার বাহু থেকেই বিভিন্ন তরঙ্গে শব্দ ধ্বনিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন লয়ে। একে অপরকে শুনতে পায় না তারা। চায়ও না হয়ত। তরঙ্গরা ভেসে যায় সরোবরের ওপরের ধূমাকাশে, মিশে যায় সরোবরের জলস্তরে।
পঞ্চম বাহু জনমনুষ্যহীন। কিছুটা দুর্গম, শ্বাপদসঙ্কুল। সেখানে জলপান করতে আসে অরণ্যের সন্তানেরা, হিংস্র বন্য প্রাণীরা আসে শিকারের খোঁজে। মাঝে মাঝে নিষাদরা যায়– এইসব প্রানীদের কাউকে যদি হত্যা করে আনা যায়। হরিণের চর্ম হলে মূল্য কম, কিন্তু আহার্য মাংস পাওয়া যাবে। বাঘের চর্ম হলে মূল্য বেশি। কোনো প্রাণীর শৃঙ্গ এবং অস্থিও বিক্রি হয় চড়া মূল্যে। এই পঞ্চম বাহুর চিরহরিৎ অরণ্যে থাকে কয়েকটি বায়স পরিবার। তারা সময়ে সময়ে অন্য তিনটি বাহুর দিকে যায়। দেবীর থানে প্রসাদ মুখে তুলে নিয়ে আসে, নিষাদের অঞ্চলে থাকে হাড় অথবা মাংসের খণ্ড। শ্রমণদের ওখানে পায় কখনো পাহাড়ি ফলের টুকরো, কখন চনক অথবা গোধূম পিষ্টকের টুকরো। পরিত্যাজ্য খাদ্যের উচ্ছিষ্ট ঠিক জুটে যায় এই তিন বাহুতে গেলে। কিন্তু, সৎকারভূমির দিকে ওরা কেউ যায় না। আশ্চর্যভাবেই, বায়স পরিবারের কেউ কখনো সৎকারভূমির দিকে যায় না।
একবার সায়াহ্নের ঠিক আগে, দিনের শেষ আলো থাকতে থাকতে বায়স পরিবারের এক যুবা গিয়ে পৌঁছেছিল সৎকারভূমিতে। এক দারুহরিদ্রা বৃক্ষের শাখায় বসে সে দেখল এক শ্রমণের দেহ, এবং এক নিষাদের দেহ তৃণভূমিতে শায়িত। দুটি দেহই নিথর, দুটি দেহরই চক্ষু মুদিত। এখানে নিকটাত্মীয়রা সৎকারের অন্তিম প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে না। একসময়ে এখানেই রেখে দিয়ে চলে যায়। এই দেহ যাদের, তাদের পরিবারও চলে গেছে কোথাও। অপেক্ষা করছে, সৎকারকার্য সম্পন্ন হলে এসে অস্থি ভাসিয়ে দিয়ে যাবে সরোবরের তৃতীয় বাহুতে।
বায়স প্রত্যক্ষ করল– সৎকারের আয়োজন সম্পূর্ণ। এক উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা মানবী বাম হস্ত তুলে তার অঙ্গুরীয়সকল দ্বারা অদ্ভুত এক মুদ্রা ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে, এবং দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করে আছে তার বক্ষের মধ্যস্থলে। এভাবেই সে দুটি দেহ প্রদক্ষিণ করল ধীর লয়ে। দুটি দেহর পাশে এসেই বসল কিছুক্ষণ। আভূমি নতজানু হয়ে তাদের মস্তকে স্পর্শ করল নিজের মস্তক। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বায়স দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পেল– সেই মানবীর শুভ্র ঝিনুকের মতো চোখের কোণে চিকচিক করছে অশ্রু। সেই আর্দ্রতা দ্রুত শুষে নিল উপত্যকার শীতল বাতাস। ক্রমে, যথাসময়ে চিতায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল, ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠল সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসা গাঢ়-সবুজ উপত্যকায়।
জাতক বায়স গরূৎবীক্ষা কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রস্তরবৎ হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল —
‘তোমার পিতা নিত্যকর্মের মতো সৎকারধর্মে ব্রতী হন।
অথচ তোমার যে পাশমোচনের গূঢ় লীলা… আমি যে এর সাক্ষী হয়ে গেলাম ডোম-তনয়া!
এই চক্ষুদ্বয়ও কি তবে তোমার হয়ে গেল?’
ধীরে ধীরে জ্বলন্ত চিতাযুগল তিন বার প্রদক্ষিণ করে সরোবরের পাশে এসে দাঁড়াল আধিরা। উদ্দত চিবুক, আকাশের দিকে দৃষ্টি… তখন জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়েছে। পূর্ণচন্দ্র।
পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্ব… মৃদুমন্দ দুলছে সরোবরের রূপালী জলতরঙ্গে। পূর্ণচন্দ্রের দিকে ঠোঁট ফাঁক করে তাকিয়ে রইল বায়স গরূৎবীক্ষা। তার ডানা তখনো ভারী হয়ে আছে। এখান থেকে পঞ্চম বাহুর দিকে এখন আর ফেরা সম্ভব নয়