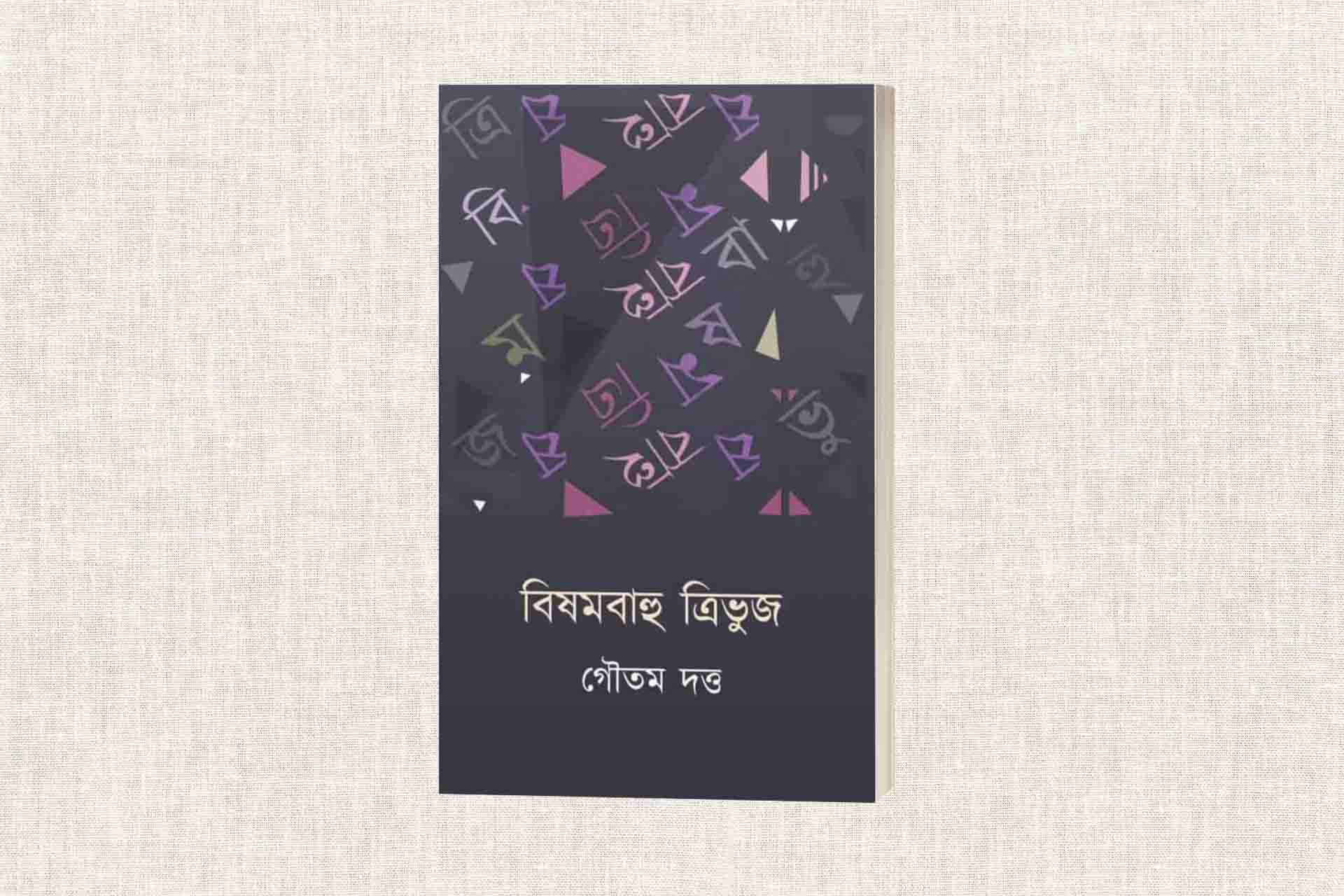বাংলা ছোটগল্পের ধারাটি যে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ এবং প্রতিনিয়ত আরও সমৃদ্ধিশালী হয়ে চলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রজন্মের উত্তোরণের সঙ্গে সঙ্গে লেখার আঙ্গিক, ভাষার মোচড়, বিষয়ের নতুনত্ব বা অভিনবত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে, কাহিনি-প্লট-ন্যারেটিভ তার পরিস্থিতির বিচারে নিজেকে অভিযোজিত করে নেয় সচেতনভাবেই। গৌতম দত্ত’র প্রথম গল্প-সংকলন “বিষমবাহু ত্রিভুজ” এই ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন তো বটেই, বরং, এই ক্ষীণতনু বইটি প্রমাণ করেছে, অল্প পরিসরেও কীভাবে মার্জিত স্বরে, অকম্পিত চেতনায় কন্টেন্টকে ঋদ্ধ করে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হতে হয়। বইটির বারোটি গল্প স্বভাব-বৈচিত্র্যে পৃথক; নতুন কিছু দেওয়ার আশ্বাস লক্ষ্যণীয়। চমকের থেকেও বেশি যা প্রাণিত করে, তা হল গল্পগুলির গল্প হয়ে ওঠার সৎ প্রচেষ্টা। প্রাঞ্জল গদ্যে বিষয়কে শানিয়ে তুলে গল্পগুলিকে সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তুলেছেন লেখক। এবার এক এক করে গল্পগুলির ময়নাতদন্ত সেরে ফেলা যাক।
প্রথম গল্প ‘একলব্য’। নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে পৌরাণিক আখ্যানটি নাড়া দেয়, তার থেকে এই গল্প একেবারেই আলাদা। রাজনৈতিক প্রেক্ষিতকে সতর্কভাবে ব্যবহার করে হিরো-অ্যান্টি হিরো বিভ্রান্তিমূলক দ্বন্দ্ব এবং আদর্শবাদের চোরাগোপ্তা অভিসন্ধির পক্ষপাত নির্মাণ করা হয়েছে। পুরাণে একলব্য গুরুবঞ্চিত বটে, কিন্তু এই গল্পে সে গুরুর সান্নিধ্য পায়, এবং দেখা যায়, গুরু তাকে সহায়তাই করেন অন্যায়ের সমুচিত শাস্তি-প্রদানে। আসলে গল্পটি আমাদের হতে-চাওয়ার গল্প, এখানে আইন গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং চিরাচরিত উচ্চ-স্বরে অন্যায়ের প্রতিবাদকে, নির্মেদ এবং যথাযথ ভাষার মোড়কে হাতিয়ার করা হয়েছে। একটিই সমস্যার জায়গা, ফ্ল্যাশব্যাক টেকনিকে ছোটগল্পের একমুখিনতাকে রক্ষার চেষ্টা হয়েছে বটে, তবে সমাজের আপাত-অনাঘ্রাত জগতটির যে আরেকটু বিস্তারিত নির্মাণ দরকার ছিল, সেখানেই এই আখ্যান খানিক মনোলিথিক মনে হয়েছে। অধ্যায়ের ব্রেকগুলি আরেকটু সন্তর্পণে করা যেতে পারত বলে মনে হয়েছে।
দ্বিতীয় গল্প, নাম-গল্প ‘বিষমবাহু ত্রিভুজ’। আবার একটি আন্ডারওয়ার্ল্ডের সৌখিনতা, তবে প্রতিশোধ এখানে মূল বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু সেই প্রতিশোধের পরত কিছুটা অন্য। শুধু কি লিবিডো? না। শুধু কি অহং? তাও না। আসলে উগ্র পুরুষতান্ত্রিকতার যে দাম্ভিকতা, তাতে আঘাত লাগার গল্প। এবং, সেই প্রতিশোধের বিরুদ্ধে যখন দাঁড়িয়ে থাকে নিষ্পাপ সতেজতা, তখন মুখ থুবড়ে পড়ে তথাকথিত শভিনিস্ট খোলস। শেষাংশটি আরোপিত হবার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকলেও লেখক সচেতনভাবে তা পরিহার করে অনেকটা অবাস্তব, কিন্তু প্রীতিকর অবস্থান এনেছেন। তবে, গল্পে লেখক বড্ড বেশি উপস্থিত। যদিও প্রয়োজনের খাতিরেই, তবে উচ্চগ্রামের প্রথম পুরুষ গল্পটিকে আবারও অনেকটা মনোলিথিক করে তুলেছে। শেষের ওই ফোনকলটি অহেতুক গল্পের স্বাতন্ত্র্যকে একটু হলেও ক্ষুণ্ণ করেছে বলেই মনে হয়েছে।
তৃতীয় গল্প, ‘বিক্রি নেই’। বইয়ের অন্যতম সেরা গল্প নির্দ্বিধায়। পোস্টমডার্ন আঙ্গিকে লেখা গল্প, একমুখিনতা রয়েছে, আবার চূড়ান্ত সাসপেন্স। একটা ঘটনাকে এক লহমায় ছেড়ে রেখে সেই সুতোকে আবার ধরে ফেলা, নির্দিষ্ট কোনো জঁরকে এড়িয়ে ক্লাইম্যাক্সকে এক্স-অক্ষের দিকে গড়াতে না দেওয়া, ও সর্বোপরি কোনওরকম কাহিনি গোঁজার চেষ্টা না করে নিপাট ল্যান্ডিং – অসাধারণ! সবথেকে বড় কথা, কোলরিজের যে সাসপেন্স সম্পর্কে সংজ্ঞা, “a semblance of truth…suspension of disbelief…which constitutes poetic faith” – তাকে সুচারুভাবে যত্ন-সহকারে নির্মাণ করেছেন লেখক।
চতুর্থ গল্প, ‘জল-ছবি’। ক্লিশে এবং আরোপিত হবার সহজ সম্ভাবনাকে নিস্তেজ করে চমক নির্মাণে করেছেন লেখক। ফ্ল্যাশব্যাক টেকনিকে নতুনত্ব নেই, বরং সহজ স্বাদু প্রাঞ্জল ভাষায় গল্পটিকে বোনা হয়েছে। শেষে, চমকের প্রকাশটি বড় বেশি চোখে-আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। কিছুটা আবডালে রাখা ইঙ্গিতবাহী হলে বেশি মনোগ্রাহী হতো বলে মনে হয়েছে। গল্পটিতে অনুচ্চ স্বরে অতীতযাপন আছে, পটে মায়ার অলংকার আছে। শুধু, গল্পটিকে পাঠকের মনে আরেকটু সচল করে তোলার পরিসর দিলে ভালো হতো বলে ধারণা।
পঞ্চম গল্প, ‘বকেয়া’। মৃদু রসাত্মক, অথচ মূল্যবোধের সুগভীর চিন্তন বর্তমান। গল্পটিতে বিশেষ কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্য নেই বটে, তবে সূক্ষ্ম রসের চমকপ্রদায়ী মোচড় পড়তে ভালো লাগে। গল্পের নির্মাণে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা হয়নি, তবে তাতে ধার ক্ষুণ্ণ হয়নি। মেদের অজস্র জায়গা ছিল, তাকেও লেখক পরিহার করেছেন মাপমতো। সব-মিলিয়ে একটি স্বাদু গল্প বলাই চলে।
ষষ্ঠ গল্প, ‘মেকওভার’। এক অন্তর্লীন প্রতিশোধের গল্প, তবে বয়ান একেবারেই গৃহস্থ। অল্প চরিত্রের সমাহারেও যে দোটানা তৈরি হতে পারে, সাংসারিক সূত্র যে কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে, তার একটি নিদর্শন এই গল্প। চমক আছে, তবে তা আরোপিত মনে হয় না পুরোপুরি। কারণ, পাঠ-শেষে মনে হয়, এটাই তো যেন কাম্য ছিল। পোয়েটিক জাস্টিসকে সূক্ষ্ম রসবোধের টোনে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে দিয়ে সমাজ-সচেতন একটি বার্তাও দিয়েছেন লেখক। তবে, গল্পটি শেষের দিকে আর সামান্য বিস্তার পেলে আরও সতেজ হতে পারত বলে ব্যক্তিগত অভিমত।
সপ্তম গল্প, “একজোড়া গাছপাকা আম আর একটি হনুমান”। অতীতচারণকে বর্তমানের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে জাদু-বাস্তবতার বৃত্ত রচিত হয়েছে এই গল্পে। হনুমান আর মুখ্য চরিত্রের সম্পর্কের রসায়ন পড়তে পড়তে রামায়ণে সীতা-হনুমান বৃত্তান্ত মনে পড়ে যায়। সেখানে সীতা ছিলেন বন্দিনী, প্রোটাগনিস্টও এখানে প্রায় তাই-ই। বৈসাদৃশ্যও আছে, তবে তা আলোচনায় অব্যাখ্যেয়। বাস্তব থেকে জাদু-বাস্তবের যাত্রাটায় লেখক বেশ সতর্ক, হড়কে যাবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল; তবে লেখক উৎরেছেন যথার্থভাবেই। ক্লাইম্যাক্সও একেবারেই কষ্ট-কল্পিত নয়, বরং সাসপেন্সসূচক সমাপ্তি বেশ প্রশংসনীয়। হালকা কমিক রিলিফের ব্যবহার গল্পের আখ্যানধর্মিতাকে বহুলাংশে সহযোগিতা করেছে।
অষ্টম গল্প, ‘বাবুয়া। ফিরে পাওয়ার গল্প, শিকড়ের গল্প। তবে পরিবেশনা সম্পূর্ণ আলাদা। পরিস্থিতি একেবারেই অচেনা নয়, এই ধরনের ঘটনার অভিঘাত দাগ কেটে যায় সেটাও স্বাভাবিক। গল্পটির শেষাংশে সামান্য অতিকথন আছে মনে হয়েছে। ন্যারেটরের দোদুল্যমানতা বিস্তারের সময়টাও ঠিকভাবে পায়নি বলে মনে হয়েছে। বিশেষত, যে প্রেক্ষাপটটি রচিত হয়েছে, তার নিরীখে যা হল – তা কতটা বাস্তবসম্মত, সে প্রশ্নও জাগে। তবে, গল্পটির মধ্যে যে আপাত রহস্যময়তার প্রকাশ ছিল, তার উন্মোচনের পর, বাস্তব-অবাস্তবের চক্রটা খানিক গুলিয়ে যেতেও পারে।
নবম গল্প, ‘ডিপ ফ্রিজ’। এই ধরনের গল্পের সমস্যা এই যে, অলীক অমাপতনের নিটোল ঘটনা যদি প্রেমজ অভিঘাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তখন তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জৈবিক অভিব্যক্তিকে অস্বীকার করা দুরূহ হয়ে পড়ে। গল্পটা বৃত্তের মতো একটা জায়গা থেকে এমনভাবে এসে সেই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে, যেন তা হবারই ছিল। আত্মসংকল্প ও সংযম নিয়ে প্লাবিত হবার সুযোগ থাকলেও লেখক সে সুর খানিকটা নিঃস্পৃহভাবে এড়িয়ে গেছেন, গল্পটিকেও যথাযথ ল্যান্ড করিয়েছেন। নামকরণের তাৎপর্য বেশ আকর্ষণীয়।
দশম গল্প, ‘অসুখ’। দুটো ভিন্ন তারে, অথবা একই তারের দ্বিপাক্ষিক অবস্থানে স্তিমিত হয়ে থাকা ঘটনার সূত্রদের এক জায়গায় নিয়ে এসে সম্পূর্ণ পৃথক একটি দিকে নিয়ে যাওয়া এই গল্পের উপজীব্য। ইংরেজি সাহিত্যে আমরা একটা কথা ব্যবহার করি, ‘deus ex machina’; অর্থাৎ, এমন কোনও ক্ষমতা বা ঘটনা, যা কোনও একটা আপাত-বিভ্রান্ত, নিঃসীম কোনও অন্ধকূপে হারিয়ে যাওয়া পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে। এখানেও একটি তৃতীয় চরিত্রের হাত ধরে প্রথম দুটি চরিত্র নিজেদের রাস্তা খুঁজে পায়। প্লটের আন্তরিক অভিঘাতটি খুব অপরিচিত না হলেও গল্প পরিবেশনের টেকনিকটি নান্দনিক, বয়ন সুচারু। অহেতুক মেদজর্জর করে গল্পটিকে লেখক ক্ষতিগ্রস্ত করেননি।
একাদশ গল্প, ‘১৭ই জুন’। একটা অপাপবিদ্ধ রহস্যময়তায় ঘেরা ছোট্ট গল্প। একটা নির্দিষ্ট দিনকে নেপথ্যে রেখে ক্রিকেটের যে ঘটনাটি আনা হয়েছে, সেটা সংবেদী। কিন্তু, এই গল্পের আসল জোর হচ্ছে, কুহকের আদিম স্বরটিকে প্রকাশ্যে না আনা, সেটিই এই গল্পটিকে ভালনারেবল হতে দেয়নি। শেষদিকে একটু অধিক দ্রুততায় গল্পটির অন্তর্ঘাত যেন সামান্য স্তিমিত হয়েছে, তবে তাতে গল্পের মূল সূত্রটি বিঘ্নিত হয়নি।
শেষ গল্প, ‘স্লিপিং’। সাংঘাতিক! থ্রিলার বটে, তবে এখানে থ্রিলারকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মহাজাগতিক একটা তরঙ্গের সুর গোটা গল্পে ছেয়ে আছে। একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও তার পরের পরিণতিকে ঘিরে যে আলো-আঁধারির মায়া-ব্যূহ রচনা করা হয়েছে, তার অভিঘাত অত্যন্ত তীব্র। গল্পের ভাষা সম্পদ। যেভাবে লেখাটিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, অতীতচর্বণের পূর্ণ সময় থাকলেও তাকে তুচ্ছ করে স্রেফ বর্তমানের পিচে এনে খেলা হয়েছে, তা অনবদ্য। শেষটিও তাই আরোপিত মনে হয় না; পোয়েটিক জাস্টিস হিসেবে ভাবা মোটেই কষ্ট-কল্পনা মনে হয় না।
সার্বিকভাবে, একজন লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থ হিসেবে এই গল্পের বইটির মধ্যে চূড়ান্ত পরিণতিবোধ ও সংযমের মিশেল বর্তমান। গল্পগুলি বিষয়-বৈচিত্র্যে একে অপরের থেকে পৃথক, চেষ্টার মধ্যে ভণিতা নজরে পরেনি। লেখকের ভাষা তাঁর সম্পদ; অত্যন্ত স্থিতধী ন্যারেটিভে গল্পগুলি রচিত। স্রেফ গোল গল্প নয়, একেকটা গল্পের অপ্রকাশ্য চিন্তন রীতিমতো ভাবার অবকাশ তৈরি করে। ছিমছাম, অনাড়ম্বর একটি বইয়ের কাছে বাংলা ছোটগল্প তার নতুন একটি দিশা পাবার আশা পায় – এ-তুল্য আনন্দের আর কিছুই নেই।
গ্রন্থঃ বিষমবাহু ত্রিভুজ
গ্রন্থকারঃ গৌতম দত্ত
প্রকাশকঃ অবগুণ্ঠন
প্রচ্ছদঃ অর্পণ
মুদ্রিত মূল্যঃ ২০০ টাকা